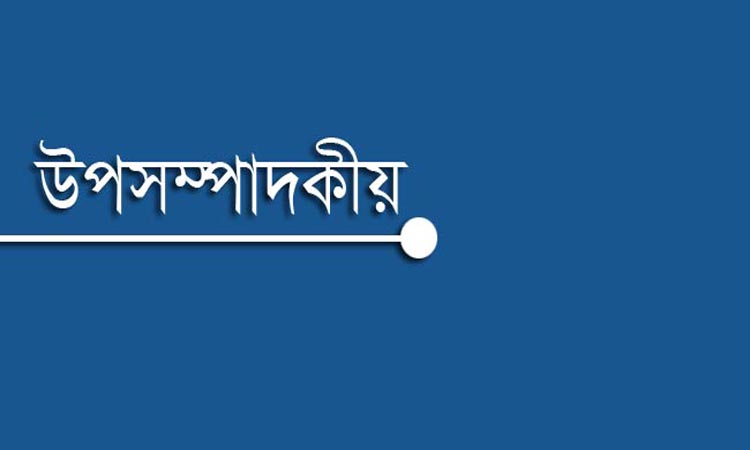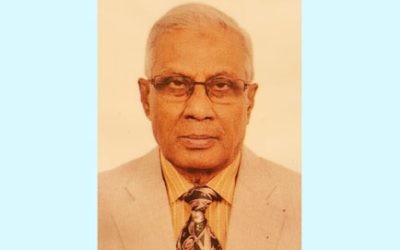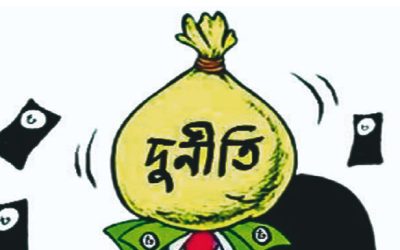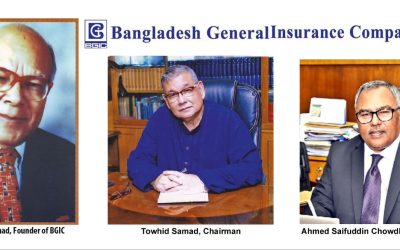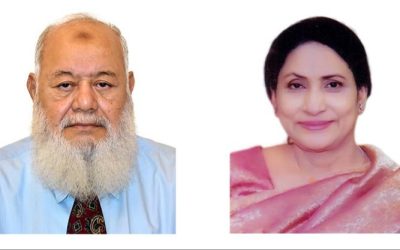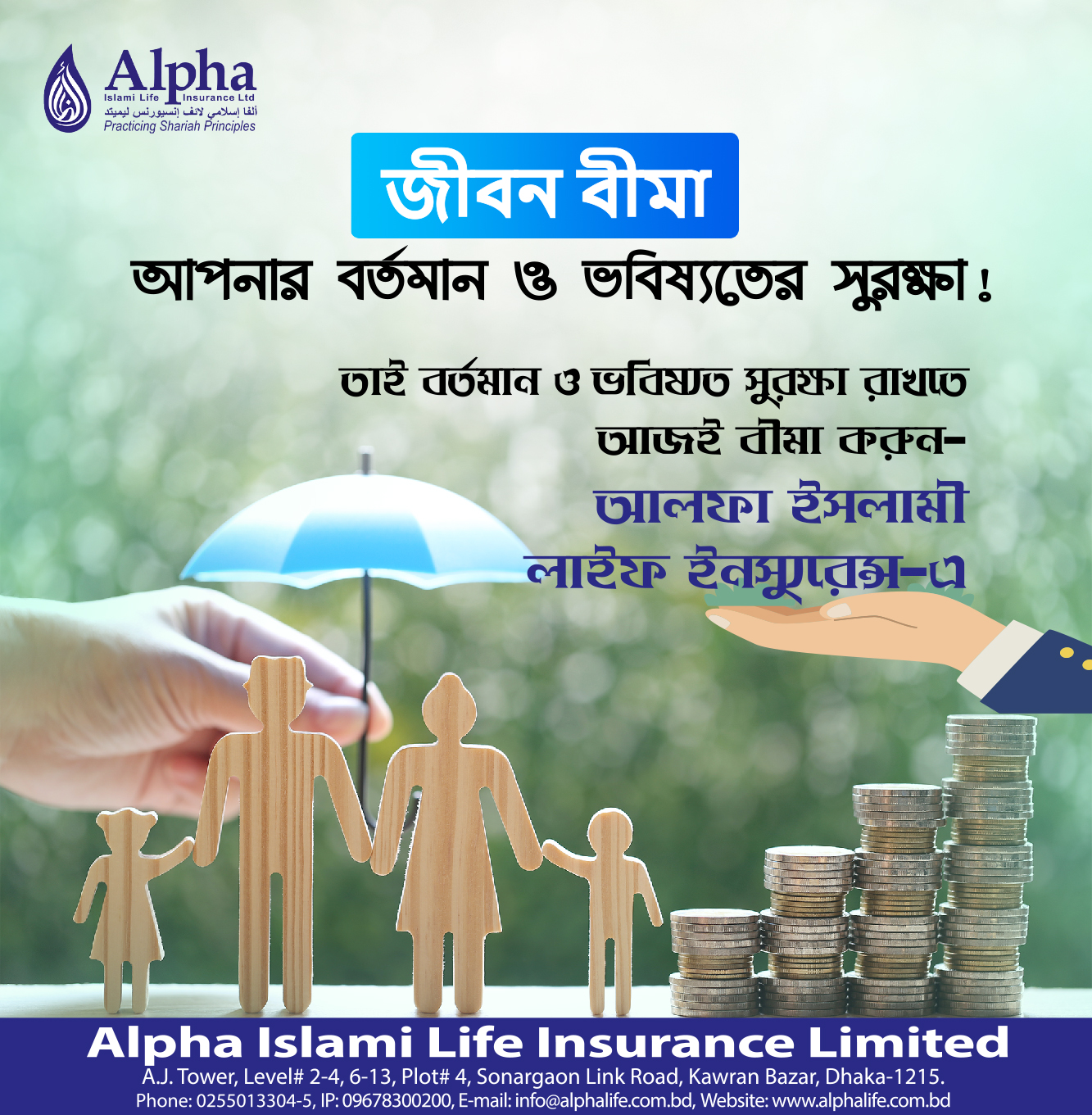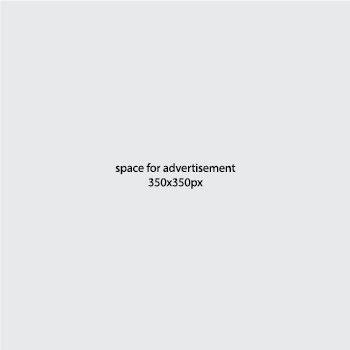রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপনকালে বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নির্দেশনা দিয়েছেন ব্যাংক ও আর্থিক খাত সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, আর্থিক খাতের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা মোটেও ভালো নেই। তাই অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক সংশ্লিষ্টগণ এই খাতের ব্যাপক সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে আসছেন অনেক দিন ধরেই। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেনো যেনো ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সংস্কারের ব্যাপারে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। শুধু তাই নয়, মহল বিশেষকে অনৈতিক সুবিধা দেবার জন্য ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মানের আইনগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনভাবে আইনগুলো পরিবর্তন এবং সংস্কার করা হয়েছে যাতে এই খাতের সমস্যাগুলো আরো তীব্রতর হয়। অনেকেই বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং সেক্টরে যে আইনি পরিবর্তন করা হয়েছে তা এই খাতের জন্য ভবিষ্যতে বিপর্যয় ডেকে আনবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে তা যাচাই বাছাই করে বাতিল করার এখনই সময়।
রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার পর বাংলাদেশ ব্যাংক যেনো নড়েচড়ে বসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে নিয়মিত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বেশ কিছু কথা বলেছেন যা তিনি আগে কখনোই বলেননি। তার বক্তব্যে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যাংক সম্ভবত ব্যাংকিং সেক্টরের সংস্কারের জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। গভর্নর উপস্থিত ব্যাংকারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অধিকতর সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভুত করার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। তার এই বক্তব্য বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। অতীতে বারবার এ ধরনের দাবি বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি। এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যেহেতু এমন আলোচনা শুরুর কথা বলেছেন তাই বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) এর নিকট থেকে যে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের অনুমোদন পেয়েছে তার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা। কাজেই সে বিবেচনায়ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ ধারনা করা যেতে পারে, দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অচিরেই হয়তো বড় ধরনের সংস্কার কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, কখে না দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না। দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা আজ খাদের কিনারে চলে গেছে। তাই কিছু একটা করা ছাড়া এই খাতকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। সামগ্রিকভাবে এই খাতটি বিপর্যয়ের কাছাকাছি রয়েছে। এর মধ্যে ১০ থেকে ১২টি ব্যাংক খুবই নাজুক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এগুলোর অস্তিত্ব নিয়েই সংকট দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কয়েকটি ব্যাংকে অর্থ যোগান দিয়ে কোনো মতে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই তাদের নিজস্ব সক্ষমতার বলে টিকে থাকতে হবে।
এখন প্রশ্ন হলো, দেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে কিভাবে বাঁচানো যাবে? বা বাঁচানোর জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই মনে করেন দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। ভারতের মতো বিশাল দেশে যেখানে ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র ২৮/২৯টি সেখানে বাংলাদেশে ব্যবসায়রত ব্যাংকের সংখ্যা হচ্ছে ৬১টি। ১৭ কোটি মানুষের দেশে ৬১টি ব্যাংক ব্যবসায়রত থাকা সত্বেও দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের বাইরে রয়ে গেছে। ব্যাংকগুলো সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। দেশের ব্যাংকগুলো সেবার ভিন্নতা আনায়নের ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। একই ধরনের সেবা নিয়ে ব্যাংকগুলো গ্রাহকের দুয়াওে যাচ্ছে। তারা নতুন এবং আকর্ষণীয় সেবা উদ্ভাবনেব ক্ষেত্রে তেমন একটা সাফল্য দেখাতে পারছে না। ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অর্থে চলে না। ব্যাংক চলে আমানতকারিদের অর্থের উপর নির্ভর করে। প্রশ্নাতীত বিশ^াস এবং আস্থা অর্জন ব্যতীত কোনো ব্যাংকই সাধারণ মানুষের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারে না। যেখানে মানুষের বিশ^াস প্রশ্নাতীত হয় না সেখানে কেউ আর্থিক লেনদেন করতে চান না। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশের ব্যাংকিং সেক্টর এখানো সাধারণ গ্রাহকের প্রশ্নাতীত বিশ^াস ও আস্থা অর্জন করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই ব্যাংকিং সেক্টরে এমন সব দুর্নীতি আর অনিয়মের খবর শোনা যায় যা মানুষের বিশ^াস ও আস্থার ভীত নাড়িয়ে দেয়। কথায় বলে, ‘মানুষ পিতৃ শোক দু’দিনে ভুলে যায় কিন্তু অর্থ হারানোর শোক সারা জীবনেও ভুলতে পারে না।’ গত বছর একটি শীর্ষস্থানীয় ইসলামি ধারার ব্যাংক থেকে উদ্যোক্তারা ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেবার খবর প্রকাশিত হলে দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ব্যাংকিং সেক্টর দেউলিয়া হতে চলেছে। এই গুজবে প্রভাবিত হয়ে আমানতকারিরা অন্তত ৫০ হাজার কোটি টাকা কয়েক দিনের মধ্যে উত্তোলন করে নেয়।
বিশে^ দু’ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইউনিট ব্যাংকিং এবং অন্যটি ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে ইউনিট ব্যাংকিং। আর বৃটেন যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু আছে তা ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং নেচারের। ইউন্টি ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে সেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে সামান্য কিছু শাখা নিয়ে একটি ব্যাঙক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউনিট ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্টচেয়ে দুর্বলতা হচ্ছে কোনো কারণে একটি বা দু’টি শাখা বিপর্যস্ত হলে পুরো ব্যাংক ধ্বসে পড়তে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাঝে মাঝেই ব্যাংক দেউলিয়া হবার খবর পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত ব্যাংক দেউলিয়া হয় বিশে^র সব দেশ মিলেও তা হয় না। ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সামান্য কিছু ব্যাংক স্থাপিত হয়। তারা বিপুল সংখ্যক শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা হচ্ছে কোনো কারণে কিছু শাখা বিপর্যস্ত হলেও পুরো মাদার ব্যাংকের কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশ বৃটিশ ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু দেশে ব্যঅংকের সংখ্যা এত বেশি হয়েছে যে, এই ব্যবস্থাকে পিওর ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং যেমন বলা যায় না তেমনি ইউনিট ব্যাংকিংও বলা যায় না। সর্বশেষ একযোগে যখন ব্যক্তি খাতে যখন ৯টি ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয় তখন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছিলেন, ‘দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। তারপরও রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হলো।’ ব্যাংকের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান যারা মানুষের বিশ^াস এবং আস্থার উপর নির্ভর করে ব্যবসায় পরিচালনা করে তা কখনোই রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া উচিত নয়। রাজনেতিক বিবেচনায় যেসব ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল তার অনেকগুলোই এখন আর ভালো ভাবে চলছে না। চরিত্রগত ভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইউনিট ব্যাংকিং নয়। আরা ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং ব্যবস্থাও নয়। এটা আসলে এক ধরনের মিশ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলো যেভাবে চলছে তাকে কোনো বাবেই সমর্থন করা যায় না। তাই বিকল্প ভাবনার সময় এসেছে।
ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সংস্কার এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার জন্য কিছু কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমেই অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অস্তিত্বের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক ধরনের দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টর দেখাশুনার দায়িত্বে থাকলেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ব্যাপারে তারা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেভাবে তদারকি করতে পারে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বেলায় তা পারে না। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ব্যাংকিং সেক্টর পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো শক্তিশালি এবং দক্ষ করে তোলা যেতে পারে।
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এত বেশি সংখ্যক ব্যাংক রাখার কোনো আবশ্যকতা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি ট্রেজারি ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংককে রেখে অবশিষ্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে যতটা সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যেতে পারে। স্টক মার্কেটের মাধ্যমে বাজারে শেয়ার ছেড়ে এসব ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। ব্যক্তি মালিাকানায় যেসব দুর্বল ব্যাংক আছে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে বলা যেতে পারে তোমরা এই সময়ের মধ্যে যদি লাভজনকতা অর্জন করতে না পারো তাহলে অন্য কোনো ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করে দেয়া হবে। অথবা বিলুপ্ত করে দেয়া হবে।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে সরকার দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। একটি রাজনৈতিক সরকার তার পছন্দনীয় দলীয় লোকদের কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেবেন এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে অযোগ্য এবং দুর্নীতিবাজদের কোনো নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্ভাব্য পরিচালনা বোর্ড সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য শীর্ষ নির্বাহীদের পৃথক তালিকা তৈরি করতে পারে। এই তালিকা থেকে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা বোর্ড সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তালিকা প্রণযনের সময় দলীয়য বিবেচনা নয় যোগ্যতা এবং সততাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।
সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ হিসাব অবলোপন নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়েছে, যা ঋণ খেলাািপদের স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত। আগে কোনো ঋণ হিসাব মন্দমানে শ্রেণিকৃত হবার পর ৫ বছর অতিক্রান্ত হলে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়েরপূর্বক শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি খেলাপি ঋণ অবলোপন করা যেতো। পরিবর্তিত আইনে কোনো ঋণ হিসাব মন্দমানে শ্রেণিকৃত হবার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হলেই তা অবলোপন করা যাচ্ছে। এ জন্য শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণের কোনো আবশ্যকতা নেই। ৫ লাখ টাকার কম ঋণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়েরের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। এতে ঋণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঋণ হিসাব অবলোপন অর্থ ঋণ মাফ করে দেয়া অথবা দাবি প্রত্যাহার নয়। ঋণ হিসাব অবলোাপনের অর্থ হচ্ছে ব্যাংকের মূল লেজার থেকে সংশ্লিষ্ট ঋণের হিসাব অন্য লেজারে সংরক্ষণ করা। এতে কৃত্রিমভাবে ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো যায়। আগে কোনো ঋণ হিসাব মোট তিনবার পুন:তফসিলিকরণ করা যেতো। এ জন্য প্রথমবার ঋণ হিসাব অবলোপনের জন্য মোট ঋণের ১০শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে ব্যাংকে জমা দিতে হতো। কয়েক বছর আগে ২শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এক বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১০বছরের জন্য ঋণ হিসাব পুন:তফসিলিকরণের সুযোগ দেয়া হয়। যারা ঋণ হিসাব অবলোপন করেছেন তারা নির্ধারিত সময়ের পর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকে আগে একই পরিবার থেকে একযোগে দুই জন পরিচালক নিয়োগের বিধান ছিল। তারা ধারাবাহিকভাবে দুই টার্ম(প্রতি টার্ম ৩ বছর করে) দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। এই আইন পরিবর্তন করে এক পরিবার থেকে একই সময়ে ৪জন পরিচালক নিয়োগের বিধান করা হয়েছিল। তারা অব্যাহতভাবে তিন টার্ম দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কিন্তু আইএমএফ’র শর্তের কারণে একই পরিবার থেকে তিনজন পরিচালক নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। এই আইন পরিবর্তন করে পূর্বের মতো এক পরিবার থেকে একযোগে সর্বোচ্চ ২জন পরিচালক নিয়োগের বিধান করা যেতে পারে।
সম্প্রতি দেশের ব্যাংকগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে নামের পেছনে ‘প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি’ যুক্ত করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের নামের শেষে ‘পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি’ শব্দ যোগ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এই নতুন নামের সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ‘প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি’ শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ করে লিখছে, পিএলসি। আবার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শব্দের সংক্ষিপকরণ করে লিখছে, পিএলসি। এই অবস্থা সাধারণ মানুষ, যারা ব্যাংকের মালিকানাগত চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত নন তারা কিভাবে বুঝবেন, কোন্ পিএলসি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর কোন্ পিএলসি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি? অথচ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ করা যেতো পিআরএলসি আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা লেখা যেতো পিইউএলসি।
আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ ব্যাংক কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। এই সেক্টরটি সঠিকভাবে না চললে পুরো অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।